সাংস্কৃতিক, প্রজন্মগত ও নৈতিক উন্নয়ন জরুরি কেন?
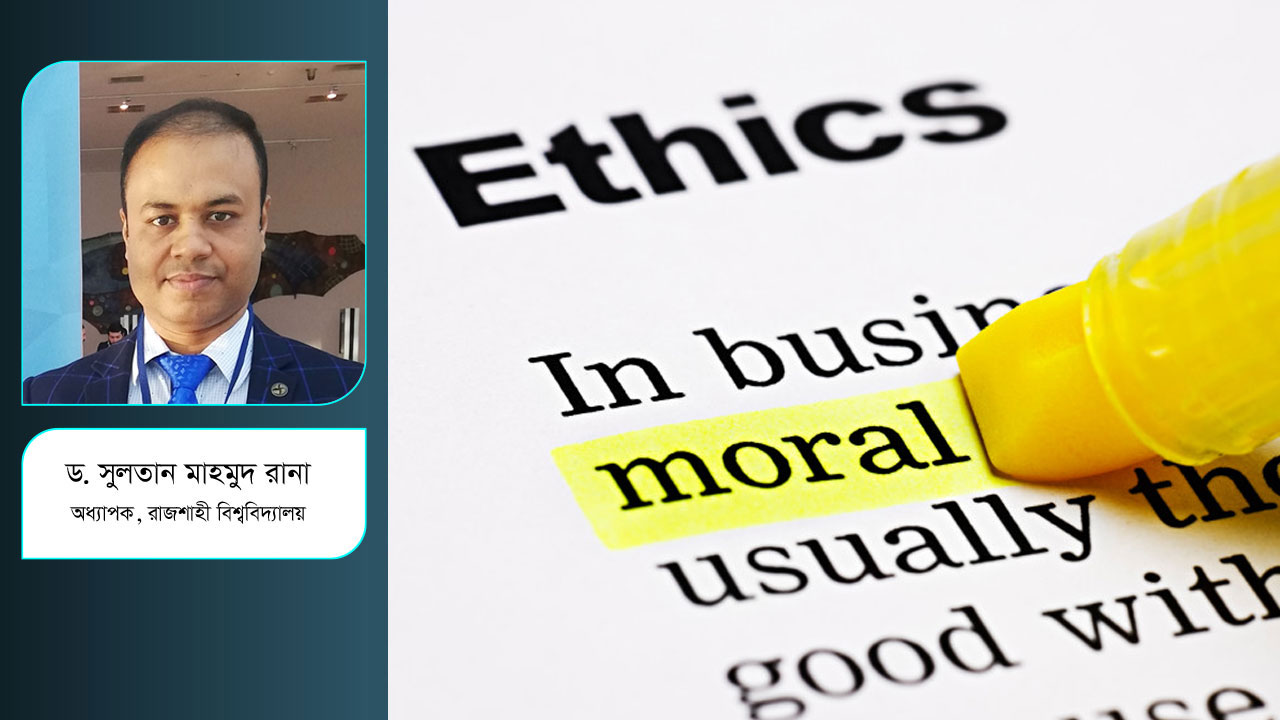
সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, প্রজন্মগত অগ্রগতি এবং নৈতিক বিকাশ একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মৌলিক স্তম্ভ। এই তিনটি অঙ্গীভূত উপাদান একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ ও মতামতের আলোকে এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সংস্কৃতি হলো একটি জাতির আত্মার প্রতিফলন। এটি শুধু শিল্প, সাহিত্য, সংগীত বা ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সমাজের জীবনযাপন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভ্যাসের সমন্বিত রূপ। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, প্রচার এবং আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া।
সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও নীতিবিদদের মতে, একটি জাতির উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের ওপরও নির্ভরশীল। তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড টেইলর (Edward Taylor) সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অন্যান্য দক্ষতা ও অভ্যাসের সমন্বিত রূপ’ হিসেবে।
সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি দেশ তার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে। এটি সমাজের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি এবং জাতীয় পরিচয় তৈরি করে। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ভাষা ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ।
দার্শনিক এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said) তার ‘Orientalism’ বইতে দেখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক পরিচয় কীভাবে গঠিত হয় এবং কীভাবে উপনিবেশবাদ সাংস্কৃতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া পিয়েরে বোর্দিউ (Pierre Bourdieu) তার ‘Cultural Capital’ তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সংস্কৃতি একটি সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর অংশ। যারা সংস্কৃতি ও জ্ঞান অর্জন করে, তারা সমাজে নেতৃত্বের আসনে বসে।
সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও নীতিবিদদের মতে, একটি জাতির উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের ওপরও নির্ভরশীল।
উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বাঙালির ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। এই ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শুধু অতীতকে স্মরণ করেই থেমে থাকে না, বরং এটি আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি তৈরি করে। যেমন, বাংলাদেশের সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন লক্ষণীয়।
প্রজন্মগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় একটি দেশের নতুন প্রজন্মের শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন। এটি একটি দেশের ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে। তাত্ত্বিক জঁ পিয়াজে (Jean Piaget) এবং লেভ ভাইগোটস্কি (Lev Vygotsky)-এর মতে, শিশু ও যুবকদের জ্ঞানার্জন এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রজন্মগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা শুধু জ্ঞান প্রদানই করে না, বরং এটি ব্যক্তির মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। তাত্ত্বিক জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন, ‘শিক্ষা হলো জীবন, জীবনই শিক্ষা।’ অর্থাৎ, শিক্ষা শুধু স্কুল বা কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।
প্রজন্মগত উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা। অমর্ত্য সেনের মতে, উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বোঝায় না, বরং এটি মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা বিকাশের সুযোগ তৈরি করা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
প্রজন্মগত উন্নয়ন বা প্রজন্মান্তরে উন্নয়ন (Intergenerational Development) হলো এমন একটি ধারণা যা সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।
উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রজন্মগত উন্নয়নকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বলে মনে করেন। তাদের মতে, সরকারের ভূমিকা হলো ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে প্রতিটি প্রজন্ম নিজের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারে।
আরও পড়ুন
উদারনৈতিক দর্শনে প্রজন্মগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রজন্মগত উন্নয়নকে সমষ্টিগত কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বলে মনে করেন। তাদের মতে, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে এক প্রজন্মের উন্নয়ন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাধা সৃষ্টি না করে।
সমাজতান্ত্রিক দর্শনে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা এবং সম্পদের সমবণ্টনের ওপর জোর দেওয়া হয়। পরিবেশবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রজন্মগত উন্নয়নকে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেন। তাদের মতে, বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়ন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।
এই দর্শনে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত নীতির ওপর জোর দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রজন্মগত উন্নয়নকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বলে মনে করেন। তাদের মতে, নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা প্রজন্মগত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
প্রজন্মগত উন্নয়ন নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দর্শন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে। এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলোও বিবেচনা করে। প্রতিটি দর্শনই প্রজন্মগত উন্নয়নের জন্য নিজস্ব পথ ও কৌশল প্রস্তাব করে, যা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
নৈতিক উন্নয়ন একটি সমাজের মূল ভিত্তি তৈরি করে। এটি ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বিকাশ করে। তাত্ত্বিক লরেন্স কোহলবার্গ (Lawrence Kohlberg)-এর মতে, নৈতিক বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তির বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়। তিনি নৈতিক বিকাশের ছয়টি স্তর বর্ণনা করেছেন, যা ব্যক্তির নৈতিক চিন্তা ও আচরণের উন্নয়নকে নির্দেশ করে।
নৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার হলো নৈতিক শিক্ষার প্রথম স্কুল, যেখানে শিশু ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শেখে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহনশীলতা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ এবং আইনকানুন নাগরিকদের নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে। নৈতিক উন্নয়নের অভাবে সমাজে অনৈতিকতা, দুর্নীতি এবং অপরাধ বৃদ্ধি পায়।
তাত্ত্বিক এমিল ডুর্খেইম (Émile Durkheim)-এর মতে, সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়ে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই, নৈতিক উন্নয়ন শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য অপরিহার্য। প্লেটো (Plato)-এর মতে, নৈতিক উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি তার ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন।
প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, নৈতিকভাবে উন্নত নাগরিকরাই একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। তিনি দার্শনিক রাজার ধারণা দিয়েছেন, যিনি নৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন। অ্যারিস্টটল (Aristotle) নৈতিক উন্নয়নকে ব্যক্তির সদগুণ (Virtue) অর্জনের সাথে যুক্ত করেছেন। তার মতে, নৈতিক সদগুণের বিকাশ ব্যক্তিকে ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তিনি ‘পলিটিক্স’ গ্রন্থে বলেছেন যে, একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে তার নাগরিকদের নৈতিক ও নাগরিক গুণাবলির ওপর।
প্রজন্মগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা শুধু জ্ঞান প্রদানই করে না, বরং এটি ব্যক্তির মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।
ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)-এর নৈতিক দর্শন নৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নৈতিক আইন ও কর্তব্যজ্ঞান (Categorical Imperative) ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করে। কান্টের মতে, নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন অসম্ভব, কারণ এটি ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের ভিত্তি তৈরি করে।
জন রলস (John Rawls) তার ‘ন্যায়ের তত্ত্ব’ (Theory of Justice) গ্রন্থে নৈতিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য দুটি মূল নীতির প্রস্তাব করেন—স্বাধীনতার নীতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ন্যায্য বণ্টন। রলসের মতে, নৈতিক উন্নয়ন ন্যায়সঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
সাংস্কৃতিক, প্রজন্মগত ও নৈতিক উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রজন্মগত উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে। একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় পরিচয় ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।
অন্যদিকে, প্রজন্মগত উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও দক্ষতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয় করে। নৈতিক উন্নয়ন সাংস্কৃতিক ও প্রজন্মগত উন্নয়নের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। নৈতিক মূল্যবোধ একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তৈরি করে। নৈতিক উন্নয়নের অভাবে সাংস্কৃতিক ও প্রজন্মগত উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, একটি সমাজে যদি নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকৃত হতে পারে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ ও মতামতের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই, প্রতিটি দেশের উচিত সাংস্কৃতিক, প্রজন্মগত ও নৈতিক উন্নয়নের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং এই তিনটি ক্ষেত্রে সমন্বিত নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।
ড. সুলতান মাহমুদ রানা ।। অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com
