রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে রাষ্ট্র, সমাজ ও সার্বভৌমত্ব
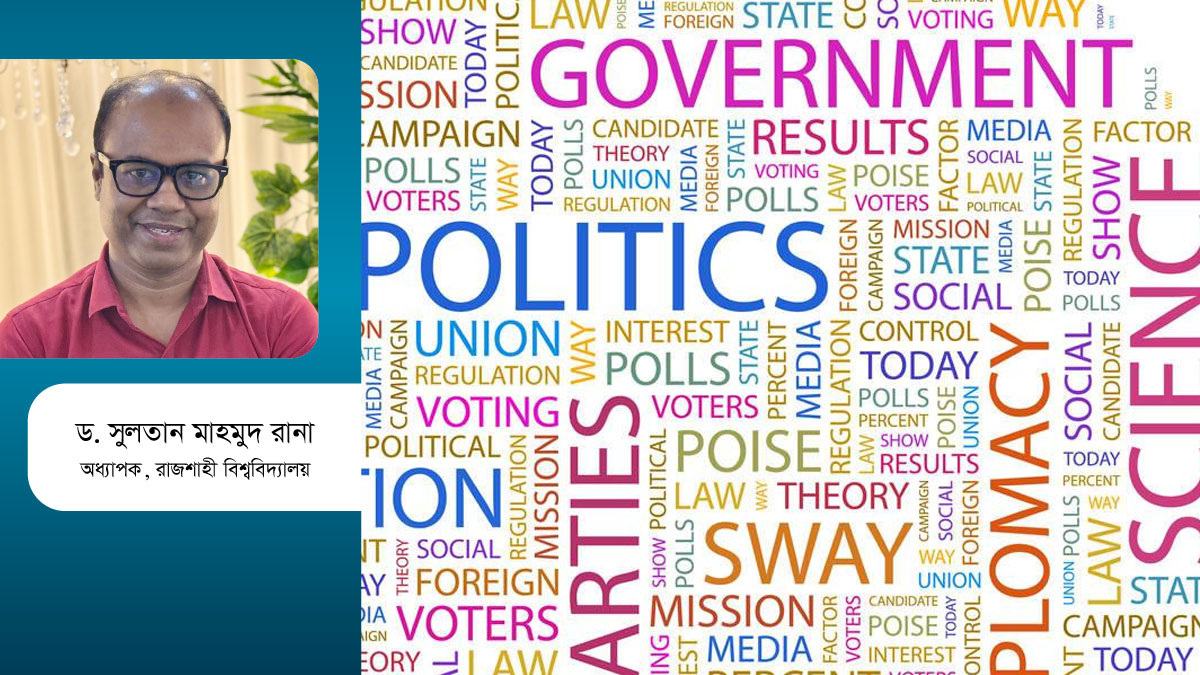
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক বলেন, ‘আইনের শাসন ছাড়া কোনো সমাজই টিকে থাকতে পারে না।’ এজন্য তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে যেকোনো রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয় এবং আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তিও নিশ্চিত করা যায়।
এরিস্টটল (Aristotle) মনে করেন, যে রাষ্ট্রে আইনের সার্বভৌমত্ব, জনগণের স্বাধীনতা এবং সংবিধানের প্রাধান্য থাকে সে রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায়। সংবিধানের প্রাধান্য না থাকলে আইনের সার্বভৌমত্ব থাকে না আর আইনের সার্বভৌমত্ব না থাকলে জনগণের স্বাধীনতাও থাকে না। আর এগুলো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে তাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা যায় না। কাজেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রথম শর্ত হলো, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।
আইনের শাসন বলতে বোঝায়, রাষ্ট্রের সব নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানকে আইনের কাছে সমানভাবে জবাবদিহি করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেকোনো সরকারের প্রধান দায়িত্ব। এটি শুধু বাহ্যিক হুমকি থেকে রক্ষা করার বিষয়ই নয়, বরং অভ্যন্তরীণ শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার সঙ্গেও জড়িত।
সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তিরা তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়, যাতে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। থমাস হবস (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke) এবং জাঁ-জাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau) এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা।
হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল একাকী, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত। তাই মানুষ একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে, যাতে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
হবসের তার তত্ত্বে বলেন, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। জন লক মনে করেন, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের প্রাকৃতিক অধিকার (জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি) রক্ষা করা। তিনি আইনের শাসন এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। রুশো মনে করেন, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। তিনি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেন।
আধুনিকীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যায়, যা সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধের মাত্রা কমিয়ে আনে।
সংঘাত তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও বৈষম্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। কার্ল মার্কস (Karl Marx) এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তিনি মনে করেন, সমাজে শ্রেণি সংঘাত (Class Conflict) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।
মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই সংঘাত সামাজিক অস্থিরতা ও বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। সংঘাত তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়বিচার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংঘাত কমিয়ে আনা যায়।
মানব নিরাপত্তা তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শুধু রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়, বরং নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, নাগরিকদের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়।
জন লক মনে করেন, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের প্রাকৃতিক অধিকার (জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি) রক্ষা করা। তিনি আইনের শাসন এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। এদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, আধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহ এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা যায়। এছাড়া, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সম্ভাব্য হুমকি শনাক্ত করে তা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করতে হবে।
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিদ্বেষ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য রাষ্ট্রের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করতে পারে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, ‘শান্তি ও সম্প্রীতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না।’ তাই রাষ্ট্রকে অবশ্যই সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এতে করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।
শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়। শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক সমাজে অপরাধ ও সহিংসতার মাত্রা কম থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং নাগরিকদের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করতে হবে। এছাড়া, সাইবার নিরাপত্তা, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।
আরও পড়ুন
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। অ্যাডাম স্মিথ বলেন, ‘একটি দরিদ্র রাষ্ট্র কখনোই নিরাপদ হতে পারে না।’ তাই রাষ্ট্রকে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এতে করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ দমন এবং শান্তি রক্ষা করা যায়। রুশো বলেছেন, ‘জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি।’ তাই রাষ্ট্রকে অবশ্যই নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এতে করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাষ্ট্রই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে না। বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাষ্ট্রকে অবশ্যই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। এতে করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।
সাম্প্রতিক বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার হুমকি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যারি বুজান (Barry Buzan) তার 'Security: A New Framework for Analysis' গ্রন্থে বলেন যে, নিরাপত্তার মাত্রা কেবল সামরিক নয়, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মূল্যায়ন করা উচিত।
...তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যায়, যা সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধের মাত্রা কমিয়ে আনে।
জলবায়ু পরিবর্তন জনসংখ্যা স্থানান্তর, সম্পদ সংকট ও সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। থমাস হোমার-ডিক্সন বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি ও জলবায়ু পরিবর্তন নিরাপত্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
রিয়ালিজম তত্ত্ব অনুসারে, একটি রাষ্ট্রের শক্তিশালী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। হ্যান্স মরজেনথাউ (Hans Morgenthau) বলেন, রাষ্ট্রের শক্তি ও শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। কেনেথ ওয়াল্টজ (Kenneth Waltz) তার নব্য-রিয়ালিজম তত্ত্বে বলেন যে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ আইন প্রয়োগ এবং নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা অপরিহার্য।
লিবারালিজম মতে, কেবল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোরতা নয়, বরং নাগরিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইম্মানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)-এর 'Perpetual Peace' ধারণা অনুসারে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।
রবার্ট কোহেন (Robert Cohen) ও জোসেফ নাই (Joseph Nye) বলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অভ্যন্তরীণ সংঘাত হ্রাস করতে সাহায্য করে। কন্সট্রাক্টিভিজম মতে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে না; বরং সামাজিক পরিচয়, মূল্যবোধ এবং জাতীয় সংহতির ওপরও নির্ভরশীল। আলেকজান্ডার ওয়েন্ডট (Alexander Wendt) বলেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি শক্তিশালী করা অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়ক।
এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব, আধুনিকীকরণ তত্ত্ব, সংঘাত তত্ত্ব, কার্যকরী তত্ত্ব এবং মানব নিরাপত্তা তত্ত্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। এই তত্ত্বগুলোর আলোকে রাষ্ট্রকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।
ড. সুলতান মাহমুদ রানা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com
