বিষণ্নতা : নীরব যন্ত্রণা ও সামাজিক বাস্তবতা
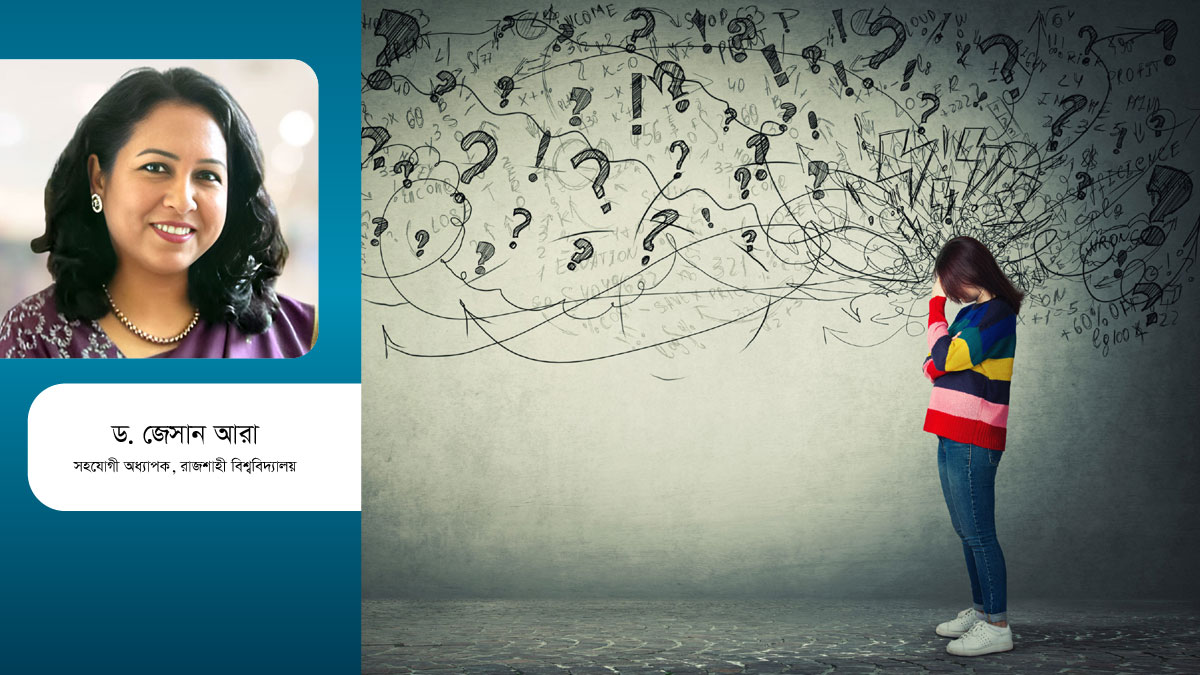
বিষণ্নতা শুধু সাধারণ মন খারাপের নাম নয়; এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা; যা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে দুঃখ, হতাশা ও আগ্রহহীনতায় ভুগতে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) মতে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত এবং এটি অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ।
সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বলছে, বাংলাদেশেও বিষণ্নতার হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, বিশেষ করে তরুণ ও কর্মজীবী মানুষের মধ্যে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৩ লাখ মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছে, যা মোট জনসংখ্যার ৬ দশমিক ৭ শতাংশ (WHO)।
বিষণ্নতা খুবই সাধারণ একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, কিন্তু এটি সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত বা এ বিষয়ে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা নেই। প্রতি পাঁচজনে একজন মানুষ জীবনে যেকোনো সময় বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতে পারে। জীবনে চলার পথে আমরা অনেকেই যেমন মাঝে মাঝে উদ্বেগে ভুগি, তেমনি মাঝে মাঝে বিষাদগ্রস্তও হই।
অনেক সময় এটি সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় না, কারণ সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার বিদ্যমান। বিষণ্নতা চিকিৎসাযোগ্য, কিন্তু অনেকেই লজ্জা, ভয় বা সামাজিক চাপের কারণে চিকিৎসা নিতে চান না। অথচ সময়মতো সঠিক সহায়তা পেলে বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
এটি একটি মানসিক রোগ এবং অন্যান্য শারীরিক রোগের মতোই চিকিৎসার প্রয়োজন। বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা এখনো সামাজিক ট্যাবু হিসেবে রয়ে গেছে। মানসিক চিকিৎসা নেওয়াকে অনেকেই দুর্বলতা বা ‘পাগল’ হওয়ার লক্ষণ হিসেবে দেখে। ফলে অনেকে সহায়তা চাইলেও লজ্জা বা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে চুপচাপ থাকেন।
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা এখনো সামাজিক ট্যাবু হিসেবে রয়ে গেছে। মানসিক চিকিৎসা নেওয়াকে অনেকেই দুর্বলতা বা ‘পাগল’ হওয়ার লক্ষণ হিসেবে দেখে। ফলে অনেকে সহায়তা চাইলেও লজ্জা বা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে চুপচাপ থাকেন।
আমরা এরকম একজনের কথা বলবো। তার ছদ্মনাম শাম্মী। সে একা থাকতে পছন্দ করত, কিন্তু একা থাকলেই যেন একটা ভারী অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরত। সকালগুলো শুরু হতো ক্লান্তি নিয়ে, যেন সে সারারাত ঘুমিয়েও কোনো বিশ্রাম পায়নি। কাজ করতে গিয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে পারত না, প্রিয় বইগুলোও আগের মতো আকর্ষণীয় লাগত না। বন্ধুদের ফোন এলে দেখেও না দেখার ভান করত। তার মনে হতো, জীবনের সব রঙ মুছে গেছে।
ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী মনে হতো, অথচ কী ভুল করেছে, সেটাই বুঝতে পারত না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হতো, তার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে, চোখের নিচে গভীর গর্ত। একদিন তার স্কুলের পুরোনো বন্ধু রনি হঠাৎ করেই দেখা করতে এলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে রনি জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে বল তো? তুই তো এমন ছিলি না!’
শাম্মী প্রথমে কিছু বলল না, কিন্তু মনে হলো, কেউ যেন প্রথমবার তার দুঃখটা বুঝতে পেরেছে। শাম্মী বলল ‘আমার আগে যে কাজগুলো করতে ভালো লাগত, এখন সেগুলোয় আর আনন্দ লাগে না। গান শুনতে ভালো লাগত, কিন্তু এখন গান চালালেই বিরক্ত লাগে। বন্ধুদের সাথেও দেখা করতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, ওরা আমাকে বুঝবে না, তাছাড়া ওদের সাথে কথা বলার শক্তিও যেন ফুরিয়ে গেছে।’
শাম্মী যে বিষণ্নতায় ভুগছে তা সে বুঝতে পারছিল না। ওর মতো এরকম অসংখ্য মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছেন, কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না যে এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা।
বিষণ্নতা ধীরে ধীরে মানুষকে গ্রাস করে। এটি কেবল দুঃখ বা একাকীত্বের অনুভূতি নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি এক মানসিক ক্লান্তি, যা ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। বিষণ্নতার প্রধান সমস্যা হলো, এটি সহজে চেনা যায় না। অনেকেই মনে করেন, বিষণ্নতা মানে কেবল কান্নাকাটি বা চরম দুঃখবোধ, কিন্তু বাস্তবে এটি আরও জটিল।
আরও পড়ুন
কেউ হয়তো সবসময় হাসিখুশি থাকছেন, স্বাভাবিক কাজ করছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছেন। বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতা বাড়ছে, এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক ও পারিবারিক চাপে অনেকেই তাদের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে পারেন না। ফলে এই অবস্থা অজ্ঞাত থেকে যায়, যা আত্মহত্যার মতো চরম পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাজীবী, গৃহিণী থেকে শুরু করে প্রবীণরাও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হচ্ছেন। শহরের দ্রুতগতির জীবনযাপন, চাকরির চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং পারিবারিক সমস্যা বিষণ্নতার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিশেষ করে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বিষণ্নতার হার বেশি দেখা যায়, কারণ তাদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি।
বাংলাদেশে এটি শুধু ব্যক্তিগত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নয়; বরং এটি সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়, যা পরিবার, সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এমন যে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। পশ্চিমা সমাজে সাধারণত মন খারাপ, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও আত্মহত্যার চিন্তাধারা হিসেবে বিষণ্নতা দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো সামাজিকভাবে সংযুক্ত সংস্কৃতিতে এটি একটু ভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে।
অনেকে সরাসরি মন খারাপের কথা না বলে শারীরিক সমস্যার কথা বলেন, যেমন মাথাব্যথা, বুকে চাপ ধরা, দুর্বল লাগা, ক্ষুধামন্দা বা ঘুমের সমস্যা। আমাদের সমাজে অনেক সময় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। অনেকে বিষণ্নতাকে ‘সৃষ্টিকর্তার পরীক্ষা’ মনে করেন বা ভাবেন যে তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাই এমন অনুভূতি হচ্ছে। ফলে তারা চিকিৎসার পরিবর্তে কেবল প্রার্থনার ওপর নির্ভর করেন।
পশ্চিমা সমাজে বিষণ্ন ব্যক্তিরা একা থাকতে পছন্দ করেন, কিন্তু বাংলাদেশের মতো পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সংযুক্ত সমাজে বিষণ্নতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বাধ্য হন। ফলে তাদের সমস্যাটি দীর্ঘদিন চাপা থাকে। আমাদের সংস্কৃতিতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে অনেকে ভয় পান, কারণ সমাজে মানসিক রোগীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। আবার যৌন নির্যাতন বা পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীরা বিষণ্নতায় ভুগলেও, সামাজিকভাবে তাদের দোষী করা হয়। ফলে তারা মানসিক সহায়তা নিতে পারেন না।
বিষণ্নতার লক্ষণগুলো হলো, সারাক্ষণ মন খারাপ বা শূন্য শূন্য লাগা, কোনো কিছুতেই আগ্রহ না পাওয়া, ঘুমের সমস্যা, অতিরিক্ত ঘুমানো বা ঘুম না আসা, শক্তিহীন বা ক্লান্ত অনুভব করা, নিজেকে দোষী মনে হওয়া, মূল্যহীন মনে হওয়া, মনোযোগ দিতে বা সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হওয়া এবং জীবনকে অর্থহীন মনে হওয়া ইত্যাদি।
বিষণ্নতার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন সম্পর্কের সমস্যা, প্রিয়জনের মৃত্যু, আর্থিক সংকট ইত্যাদি বিষণ্নতার কারণ হতে পারে। আবার নিজের প্রতি নেতিবাচক ধারণা বা কম আত্মসম্মান বিষণ্নতার কারণ হতে পারে। এছাড়াও শৈশবে নির্যাতন, অবহেলা বা অন্যান্য মানসিক আঘাত ভবিষ্যতে বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ায়।
বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতা বাড়ছে, এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক ও পারিবারিক চাপে অনেকেই তাদের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে পারেন না। ফলে এই অবস্থা অজ্ঞাত থেকে যায়, যা আত্মহত্যার মতো চরম পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অ্যালকোহল বা অন্যান্য মাদকের অপব্যবহার বিষণ্নতার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতা, সেরোটোনিন ও ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্য নষ্ট হলে বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে। এই কারণগুলো জটিল এবং ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে।
বিষণ্নতা মোকাবিলার জন্য নিজের যত্ন কার্যকর কিছু কৌশল রয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম করা, যেমন হাঁটাহাঁটি, যোগব্যায়াম বা হালকা শরীরচর্চা মস্তিষ্কে সেরোটোনিন বৃদ্ধি করে, যা মেজাজ উন্নত করে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া। প্রোটিন, ফলমূল ও সবজি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা এবং অতিরিক্ত ক্যাফেইন ও চিনি এড়িয়ে চলা। নিয়মিত রিলাক্সেশন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা, এটি মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে।
নিজেকে দোষারোপ করা বন্ধ করুন, নিজেকে সহানুভূতির সাথে দেখুন এবং নেতিবাচক চিন্তাগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করুন। ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, একবারে খুব বেশি কাজ করার চেষ্টা না করে ছোট ছোট ধাপে এগিয়ে যান। গান শোনা, ছবি আঁকা, বই পড়া বা যা আপনাকে আনন্দ দেয়, তাই করুন। প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকুন, গাছপালা বা খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ সময় কাটান। বিশ্বাসযোগ্য মানুষের সাথে কথা বলুন, যেমন, পরিবার, বন্ধু বা থেরাপিস্টের সাথে অনুভূতি ভাগ করুন।
বিষণ্নতা অদৃশ্য হলেও এটি বাস্তব। এটি মানসিক শক্তি কেড়ে নেয়। আর আত্মহত্যার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে বিষণ্নতা অন্যতম, কিন্তু এটি এখনো যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। আত্মহত্যার চিন্তা হুট করে আসে না, এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করে, ‘এই কষ্ট কখনোই শেষ হবে না,’ অথচ বাস্তবে সঠিক সহায়তা পেলে সুস্থ হওয়া সম্ভব।
কাউকে যদি বিষণ্ন মনে হয়, তবে তার পাশে থাকা, কথা বলা এবং প্রয়োজনে অবশ্যই কগনিটিভ-বিহেভিয়োরাল থেরাপি (CBT) নেওয়া, কাউন্সিলিং করা ও পেশাদার সাহায্য নেওয়াই সেরা উপায়। বিষণ্নতা এক গভীর ছায়ার মতো, কিন্তু সেই ছায়ার বাইরে আলো আছে।
বিষণ্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই একজন পেশাদার মনোবিজ্ঞানী বা থেরাপিস্টের পরামর্শ নিন। নিজের যত্ন গুরুত্বপূর্ণ, তবে চিকিৎসার বিকল্প নয়। পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে বিষণ্নতা ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় এবং এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তাই শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই নয়, বরং সামাজিক ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও বিষণ্নতা মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
ড. জেসান আরা ।। সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
jesan@ru.ac.bd
